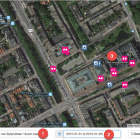English
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাংবাদিকদের জন্য এই পরিসংখ্যানগুলো খুব হতাশাজনক। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টসের সূত্রমতে, ১৯৯২ সাল থেকে, হত্যার শিকার হয়েছেন ১৩০০-র বেশি সাংবাদিক। তাঁদের মধ্যে ৭০০-র বেশি ক্ষেত্রে এই হত্যার কোনো বিচার হয়নি। হত্যাকারীকে আইনের আওতায় আনা হয়নি। আর এখন বিশ্বজুড়ে ২৫০ জনের বেশি সাংবাদিক আছেন কারাবন্দি। সেটিও এমন কাজ করতে গিয়ে, যা বিশ্বের অনেক জায়গাতেই বিবেচনা করা হয় রুটিন রিপোর্টিং হিসেবে।
আর এই পরিস্থিতি মনে হচ্ছে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে হামলা ও হত্যা; রেকর্ড পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। ম্যারি কোলভিন বা ড্যানিয়েল পার্লের মতো হাই প্রোফাইল পশ্চিমা সাংবাদিকদের হত্যাকাণ্ড আন্তর্জাতিকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত সাংবাদিকেরা স্থানীয় গণমাধ্যমে কাজ করছেন। আর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো হিমবাহের ওপরের অংশটুকু মাত্র। এর বাইরে মারধর, অপহরণ, কারাবন্দি এবং আরও অনেক ধরনের হুমকির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এগুলোও সাংবাদিকদের চুপ করিয়ে রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।
হুমকিগুলো অনেক দিক থেকে আসে। মাদক ব্যবসার গোষ্ঠী বা বিদ্রোহী গ্রুপ; স্বৈরশাসক বা জাতিগত বিদ্বেষ; বুলেট অথবা সন্ত্রাসীদের বোমা; অনেক কিছুর মধ্যেই পড়তে হয় সাংবাদিকদের। একেক জায়গায় হুমকি-নিপীড়নের ধরন একেক রকম। ফলে “একক বা সহজ সমাধান” জাতীয় কিছু নেই।
এই সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করছে বেশ কিছু পেশাজীবী সংগঠন এবং বড় কিছু বহুমাত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। যাদের মধ্যে আছে জাতিসংঘ এবং অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ।
গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্কের রিসোর্স পেজ সিরিজের অংশ হিসেবে, আমরা প্রকাশ করছি সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত এই গাইড। শুরুতেই থাকছে এ বিষয়ে এরই মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ গাইড আছে, সেগুলোর লিংক। এরপর থাকছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রধান কিছু আন্তর্জাতিক গ্রুপের লিংক, যারা কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ওপর সহিংস হামলা নিয়ে কাজ করে।
নিরাপদ থাকা এবং সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি কাভারের গাইড
কমিটি ফর দ্য প্রটেকশন অব জার্নালিস্টস সেফটি কিট: ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে সিপিজের চার পর্বের এই সুরক্ষা গাইড। এখানে শারীরিক, ডিজিটাল, মানসিক সুরক্ষার রিসোর্স ও টুলস সম্পর্কে মৌলিক কিছু তথ্য রয়েছে সাংবাদিক ও নিউজরুমগুলোর জন্য। এ ছাড়া সিপিজে প্রকাশ করেছে সুরক্ষাসংক্রান্ত কিছু প্রতিবেদন। যেমন ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ফিজিক্যাল সেফটি: সলো রিপোর্টিং এবং ফিজিক্যাল সেফটি: মিটিগেটিং সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স। দেখতে পারেন সিপিজের ইউএস ইলেকশন ২০২০: জার্নালিস্ট সেফটি কিট।
সাংবাদিকদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্র্যাকটিক্যাল গাইড। ২০১৭ সালে এটি হালনাগাদ করেছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস ও ইউনেসকো। পাওয়া যাচ্ছে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষায়।
বিক্ষোভ কাভার করার জন্য নিরাপত্তা ম্যানুয়াল তৈরি করেছে আবরাজি (দ্য ব্রাজিলিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম।) পুরো ম্যানুয়ালটি এখানে পাবেন ইংরেজিতে।
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের সুরক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালা: ২০১৫ সালে এই গাইডলাইন তৈরি করেছিল বড় কিছু কোম্পানি ও সাংবাদিকতা-সংশ্লিষ্ট সংগঠনের জোট। এটি পরবর্তীকালে অনুবাদ করা হয়েছে সাতটি ভাষায়।
নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষাসংক্রান্ত হ্যান্ডবুক। ২০১৭ সালে ৯৫ পৃষ্ঠার এই গাইড তৈরি করেছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ওমেন ইন রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন। যুদ্ধ ও সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে কাজ করা নারী সাংবাদিকদের জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে। ঝুঁকি নির্ধারণ, অনলাইন নিপীড়ন ও ভ্রমনসংক্রান্ত সুরক্ষা বিষয়ে আলাদা অধ্যায় আছে এই গাইডে।
অনলাইনে সাংবাদিকদের হয়রানি: ট্রোল বাহিনীর আক্রমণ: সাংবাদিকদের জন্য বিপজ্জনক বিষয়গুলো চিহ্নিত করা এবং তাদের সাহায্য দিতে ১২টি কার্যালয়ের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাংবাদিকদের হুমকি দেয়া হয়, ভয় দেখিয়ে চুপ করানোর জন্য। সরকার, আন্তর্জাতিক সংগঠন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সংবাদমাধ্যম ও বিজ্ঞাপনদাতারা কীভাবে এসব ক্ষতিকর অনলাইন প্রচারণার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে, সে জন্য ২০১৮ সালে ২৫টি পরামর্শ হাজির করেছে আরএসএফ। দেখুন জিআইজেএন-এর সারসংক্ষেপ।
সংবাদমাধ্যমগুলোর নিরাপত্তাসংক্রান্ত স্ব-মূল্যায়ন। এটি এসিওএস অ্যালায়েন্সের একটি টুল। যা দিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের সাংবাদিকদের জন্য নিরাপত্তাসংক্রান্ত চর্চা ও প্রটোকল যাচাই করতে পারে এবং সেটি আরও উন্নত করতে পারে। এসিওএস অ্যালায়েন্স বিভিন্ন সাংবাদিকতা-সংশ্লিষ্ট গ্রুপের একটি জোট। ২০১৯ সালের এই স্ব-মূল্যায়ন টুলটিতে আছে “কিছু প্রধান প্রশ্ন ও গাইডলাইন, যা সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে একটি গঠনমূলক আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং সেগুলো কার্যকর ও বাস্তবসম্মতভাবে কাজে লাগানোর বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবে।” (স্ব-মূল্যায়নের টুলটি এখানে পাবেন ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষায়।)
সেফ+সিকিউর ২০১৯ সালে প্রকাশ করেছে একটি হ্যান্ডবুক ও ইস্যুকেন্দ্রিক চেকলিস্ট। তথ্যচিত্র নির্মাতাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সেরা কিছু রিসোর্সের খবর আছে এখানে। একই সঙ্গে আছে এ বিষয়ে আরও তথ্য বা প্রশিক্ষণ কোথায় পাওয়া যাবে, সেই খোঁজও।
হয়রানি-হেনস্তার শিকার হওয়া সাংবাদিকদের জন্য আইপিআইয়ের ৫ পরামর্শ। ২০২০ সালে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট। অনলাইনে হয়রানির শিকার হওয়া সাংবাদিকদের কীভাবে সাহায্য-সমর্থন দেওয়া যায়, তা নিয়ে নিউজরুমগুলোর জন্য প্রটোকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে। অনলাইনে হয়রানি বিষয়ে অন্যান্য রিসোর্সও তৈরি করেছে আইপিআই।
অনলাইন হয়রানির ফিল্ড ম্যানুয়াল। ২০১৭ সালে এটি তৈরি করেছে পেন আমেরিকা। “লেখক, সাংবাদিক, তাদের মিত্র এবং চাকরিদাতারা কীভাবে অনলাইনে বিদ্বেষ ও হয়রানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারেন, তার কার্যকর কিছু কৌশল ও রিসোর্সের” হদিস রয়েছে এখানে।
গণমাধ্যমকর্মী এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ। ২০১৭ সালে এই হ্যান্ডবুক তৈরি করেছে ব্রিটিশ রেড ক্রস এবং ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড কমপারেটিভ ল (বিআইআইসিএল)।
ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের কোন জিনিসগুলো খেয়াল রাখা দরকার, তা জানিয়ে দুই পৃষ্ঠার চেকলিস্ট তৈরি করেছে দ্য এসিওএস অ্যালায়েন্স।
পরিবর্তনের জন্য রিপোর্টিং: সংকটপূর্ণ অঞ্চলের স্থানীয় সাংবাদিকদের হ্যান্ডবুক। ২০০৯ সালে এটি তৈরি করেছে ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার অ্যান্ড পিস রিপোর্টিং। এখানে একটি অধ্যায় আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে। এটি পাওয়া যাচ্ছে ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, রাশিয়ান, কাজাখ, কিরগিজ ও তাজিক ভাষায়।
দ্য সেফটি নেট ম্যানুয়াল। উপশিরোনাম: অস্বাভাবিক ও জরুরি পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের জন্য গাইডলাইন। ২০১৭ সালে এটি তৈরি করেছে সাউথইস্ট ইউরোপ মিডিয়া অর্গানাইজেশন। এটি পাওয়া যাচ্ছে ইংরেজিসহ ১১টি আঞ্চলিক ভাষায়।
দ্য জেমস ডব্লিউ. ফোলি জার্নালিস্ট সেফটি গাইড: এ কারিকুলাম প্ল্যান ফর কলেজ জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশনস ইনস্ট্রাক্টর। ২০১৪ সালের ১৯ আগস্ট সিরিয়াতে হত্যা করা হয়েছিল সাংবাদিক জেমস ফোলিকে। তাঁকে নিয়ে নির্মিত এইচবিওর একটি তথ্যচিত্রের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে পাঁচ সেশনের এই কোর্স। এই শিক্ষা কার্যক্রমে আছে অনেক রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল। বিশেষত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রবন্ধ। যেগুলোতে পরিবেশ-পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং নানাবিধ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। “FoleySafety” এই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এখানে অংশ নিতে পারবেন।
মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশনের সময় কীভাবে শনাক্ত করবেন অন্যদের দ্বারা সংক্রামিত মানসিক চাপ এবং কীভাবে সেটি কাটিয়ে উঠবেন, ২০১৮ সালে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন হান্না ইলিস। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্কম্যান ক্লাইন সেন্টার ফর ইন্টারনেট অ্যান্ড সোসাইটির গবেষণা সহযোগী।
ফ্রিল্যান্স ফাইলস: সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে কাজ করা সাংবাদিকদের জন্যও সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। ২০১৭ সালে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্টাল জার্নালিস্টসের ওয়েবসাইটে এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন ডেল উইলম্যান।
সাংবাদিকতা ও সংক্রমিত মানসিক চাপ: সাংবাদিক, সম্পাদক ও সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি গাইড। অন্যদের কাছ থেকে যে মানসিক চাপ সংক্রমিত হয়, এবং তা মোকাবিলায় যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়, তা নিয়ে বাস্তব কিছু পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ২০১৭ সালের এই হ্যান্ডবুকে। এটি লিখেছেন স্যাম ডুবারলি ও মাইকেল গ্রান্ট।
নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয় ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স মিডিয়া ফাউন্ডেশন। এখানে দেখুন তাদের রিসোর্সের তালিকা।
সাংবাদিকদের আত্ম-যত্ন, ২০১৯ সালের নিকার সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়েছিল এই “বাস্তবসম্মত গাইড”।
সাংবাদিকদের টিকে থাকার গাইড। এখানে আছে অ্যানিমেশন দিয়ে বানানো নয়টি লেসন। কীভাবে টিয়ার গ্যাস সামলাতে হবে, এমন তথ্যও আছে এখানে। ২০১২ সালে এটি তৈরি করেছিল সামির কাসির ফাউন্ডেশনের এসকিইজ সেন্টার ফর মিডিয়া অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম।
নৃশংসতা নিয়ে রিপোর্টিং। সাক্ষাৎকার নেওয়া বিষয়ে এই লেখা ২০১৪ সালে লিখেছিলেন পিটার দু টোয়িত। এখানে একটি অধ্যায় আছে “নিজের যত্ন নেওয়া” প্রসঙ্গে।
জরুরি প্রটোকল কেস স্টাডি। এটি লিখেছেন রাশিয়ান সংবাদপত্র মেডুজার অনুসন্ধানী সাংবাদিক ইভান গোলুনভ। জিআইজেসি১৯-এ তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, তাঁকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখন মেডুজা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিল।
গ্রাউন্ডট্রুথ: প্রতিনিধিদের জন্য একটি ফিল্ড গাইড। মাঠে গিয়ে সাংবাদিকদের কোন জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে ও চর্চা করতে হবে, তার একটি গাইডলাইন আছে এখানে। আরও আছে অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের প্রবন্ধ। ২০১৯ সালের এই প্রবন্ধটি দেখুন: হুমকি ও হয়রানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পাঁচটি পরামর্শ
ট্র্যাজেডি ও সাংবাদিক। ১৯৯৫ সালে এটি তৈরি করেছে ডার্ট সেন্টার ফর জার্নালিজম অ্যান্ড ট্রমা।
সাংবাদিকতার সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত গ্রুপ
আ কালচার অব সোসাইটি (এসিওএস)। ২০১৫ সালের শেষে এই জোট তৈরি হয়েছিল বড় নিউজ কোম্পানি ও সাংবাদিকতা-সংশ্লিষ্ট সংগঠনদের নিয়ে। তাদের লক্ষ্য ছিল বিশ্বজুড়ে কাজ করা ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকদের সুরক্ষা মানদণ্ড আরও উন্নত করা। নিরাপত্তাসংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান, প্রশিক্ষণ, বীমা ও যোগাযোগের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছে এই জোট।
আর্টিকেল ১৯: এটি লন্ডনভিত্তিক সংগঠন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হুমকির মুখে আসলে তা নিয়ে প্রচার-প্রচারণা ও দেনদরবার করে আর্টিকেল ১৯। এ ছাড়া তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, গবেষণা করে ও সেগুলো প্রকাশ করে। পেশাগত কারণে নিজেদের বা পরিবারের সদস্যদের জীবন হুমকির মুখে আছে, এমন সাংবাদিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রচার চালায় আর্টিকেল ১৯।
কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে): নিউইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন পরিচালিত হয় সাংবাদিকদের দ্বারা গঠিত পরিচালনা পর্ষদ দিয়ে। সিপিজে প্রতিটি দেশ ধরে ধরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক নানা মিশন পরিচালনা করে এবং সাংবাদিক নিপীড়ন ও হত্যার বিচার না হওয়ার তালিকা হালনাগাদ করে। সিপিজের জার্নালিস্ট অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম থেকে আইনি, চিকিৎসা বা অন্য কোথাও পুনর্বাসনের সহায়তা পান হুমকির মুখে থাকা সাংবাদিকেরা। একই সঙ্গে তারা সাহায্য-সহযোগিতা দেয় হত্যার শিকার হওয়া বা জেলে থাকা সাংবাদিকদের পরিবারকে।
ফাস্ট ড্রাফট তৈরি করেছে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম। যেখান থেকে নিউজরুমগুলো অনলাইন হুমকির বিরুদ্ধে প্রস্তুত হওয়াসংক্রান্ত সহায়তা পাবে। তারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
গ্লোবাল জার্নালিস্ট সিকিউরিটি। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়াশিংটনভিত্তিক এই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেন সংবাদকর্মী, নাগরিক সাংবাদিক, মানবাধিকার ও এনজিও কর্মীদের। তারা উন্নত ও উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশগুলোর নিরাপত্তারক্ষীদের প্রশিক্ষণ দেন যে কীভাবে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের মানদণ্ডগুলো মেনে চলা যায় এবং কীভাবে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে নিরাপদে লেনদেন করতে হবে।
ইন্টার আমেরিকান প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (আইএপিএ): মিয়ামি, ফ্লোরিডাভিত্তিক এই সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে। এখন তাদের সদস্যসংখ্যা ১৪০০। এবং তারা ছড়িয়ে আছে চিলি থেকে কানাডা পর্যন্ত। সংগঠনটি পুরো আমেরিকা মহাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে ও এর পক্ষে কাজ করে। কোনো সাংবাদিক হত্যার শিকার হলে তারা একটি র্যাপিড রেসপন্স ইউনিট নিয়োগ করে। প্রতিটি দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে কাজ করা সাংবাদিকদের জন্য তারা প্রকাশ করেছে একটি “ঝুঁকি মানচিত্র”। সাংবাদিক নির্যাতন বা হত্যা বিচার না হওয়ার ব্যাপারটি তারা আলাদাভাবে পর্যবেক্ষেণ করে। এ বিষয়ে এই অঞ্চলের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে তাদের “ইমপিউনিটি প্রজেক্ট”-এ।
ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস (আইএফজে): ব্রাসেলসভিত্তিক এই সংগঠন আধুনিক রূপে যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৫২ সালে। আইএফজে নিজেদের বর্ণনা দেয় পুরো বিশ্বের সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে। তারা পর্যবেক্ষণ করে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পরিস্থিতি এবং সাংবাদিকদের সুরক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে দেনদরবার করে। তারা প্রতিষ্ঠা করেছে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সেফটি ইনস্টিটিউট।
ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম অব ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ (আইএফইএক্স): টরন্টোভিত্তিক এই সংগঠনের সবচেয়ে দৃশ্যমান ভূমিকা হলো: তথ্যের সূত্র। তারা পরিচালনা করে, যাকে তারা বলে “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তারিত এবং উন্মুক্ত তথ্য সেবা”। তাদের আছে একটি সাপ্তাহিক নিউজলেটার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রবন্ধের নিয়মিত তালিকা প্রকাশ এবং বিশ্বজুড়ে তাদের সদস্যদের থেকে আসা “অ্যাকশন অ্যালার্ট”। ৫০টির বেশি দেশে ৯০টির বেশি সহযোগী সংগঠন আছে তাদের। ২০১১ সালে তারা ২৩ নভেম্বরকে ইন্টারন্যাশনাল ডে টু এন্ড ইনপিউনিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সেফটি ইনস্টিটিউট (আইএনএসআই): এটি ব্রাসেলসভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। ২০০৩ সালে এটি গড়ে উঠেছিল আইএফজে ও আইপিআইয়ের যৌথ উদ্যোগে। এটি নিজেদের বর্ণনা দেয় এভাবে: “বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করা সংবাদকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এটি কাজ করে সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিকদের সহায়তা দেওয়ার গ্রুপ ও ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত জোটের মাধ্যমে।” তারা প্রশিক্ষণ আয়োজন করে, সুরক্ষাসংক্রান্ত কৌশল-পরামর্শ ও ম্যানুয়াল তৈরি করে। এবং সাংবাদিকদের ওপর আসা যেকোনো আঘাত পর্যবেক্ষণ করে। সেটি সহিংস আক্রমণই হোক বা কোনো দুর্ঘটনা।
ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই): ১৯৫০ সালে গঠিত হয়েছিল ভিয়েনাভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান। আইপিআই নিজেদের বর্ণনা দেয় “সম্পাদক, সংবাদমাধ্যমের নির্বাহী ও অগ্রণী সাংবাদিকদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক” হিসেবে। আইএনএসআই-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, তারা পর্যবেক্ষণ করে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাসংক্রান্ত পরিস্থিতি এবং প্রকাশ করে বার্ষিক ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম রিভিউ। ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলোতে তারা নিয়মিত মিশন পরিচালনা করে এবং সাংবাদিকদের ওপর আসা হামলাগুলো চিহ্নিত করে।
রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্যারিসভিত্তিক এই সংগঠন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা লঙ্ঘনসংক্রান্ত তথ্য এক জায়গায় করে আরএসএফ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মিশনগুলোতে সহায়তা দেয়। সুরক্ষার লক্ষ্যে সংবাদমাধ্যম বা ব্যক্তি সাংবাদিকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আর্থিক সহায়তা দেয়। সহায়তা দেয় জেলে থাকা সাংবাদিকদের পরিবারকেও। কাজ করে সাংবাদিকদের সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে। বিশেষভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে। পেশাগত কাজে বিপজ্জনক জায়গায় যাচ্ছেন, এমন সাংবাদিকদের তারা বুলেটপ্রুফ ভেস্ট ও হেলমেট ভাড়া দেয় এবং বিমার ব্যবস্থা করে।
ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজপেপার এবং নিউজ পাবলিশার্স (ডব্লিউএএন-আইএফআরএ): ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্যারিসভিত্তিক এই সংগঠন। পাঁচটি মহাদেশ থেকে ১৮ হাজারের বেশি প্রকাশনার প্রতিনিধিত্ব করে ডব্লিউএএন। মৌলিক নানা বিষয়ে তথ্য ও সহায়তা প্রদান ছাড়াও ডব্লিউএএন বিশেষভাবে নজর দেয় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা পর্যবেক্ষণের দিকে। এবং তারা “দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্পেইন এবং বিশেষ ঘটনাগুলো নিয়ে প্রচারপ্রচারণা চালায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে।”
ফ্রি প্রেস আনলিমিটেড: নেদারল্যান্ডসের এই গণমাধ্যম উন্নয়ন এনজিও গঠন করেছে রিপোর্টার্স রেসপন্ড। এটি একটি আন্তর্জাতিক জরুরি তহবিল। যেখান থেকে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকে সরাসরি সহায়তা দেওয়া হয়। স্থানীয় নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়েও কীভাবে দ্রুততম সময়ে আবার কর্মকাণ্ড শুরু করা যায়, সে বিষয়ে সক্ষম করে তোলা তাদের লক্ষ্য। কোনো সহায়তার অনুরোধ এলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাড়া দেওয়ার লক্ষ্য এই গ্রুপের।
ক্যালিটি ফাউন্ডেশন: সুইডেনভিত্তিক এই তহবিল থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া হয় বিশ্বের সেসব রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের, যারা পেশাগত কারণে কারাগারে আছেন, শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছেন বা নির্বাসনে যাচ্ছেন।
লাইফলাইন ফান্ড: দ্য লাইফলাইন এমব্যাটলড সিএসও অ্যাসিস্ট্যান্স ফান্ড থেকে জরুরি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় হুমকি বা হামলার মুখে থাকা বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি গ্রুপকে। যার মধ্যে সাংবাদিকদের সংগঠনও আছে। ১৭টি সরকার ও ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায়, লাইফলাইন দিয়ে থেকে স্বল্পমেয়াদি জরুরি অনুদান। এটি তারা দেয় চিকিৎসা সহায়তা, আইনি সহায়তা, আইনি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, অস্থায়ীভাবে অন্য কোনো জায়গায় স্থানান্তর, নিরাপত্তা ও সামগ্রী প্রতিস্থাপনের জন্য।
রোরি পেক ট্রাস্ট: লন্ডনভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং তাদের পরিবারকে বাস্তবিক সাহায্য-সহযোগিতা দেয়। তাদের কর্মদক্ষতা, সুরক্ষা, নির্ভয়ে কাজ করতে পারার অধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। ফ্রিল্যান্স অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম, ফ্রিল্যান্স রিসোর্স, রোরি পেক অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে।
আরআইএসসি: রিপোর্টার্স ইনস্ট্রাক্টেড ইন সেভিং কলিগস একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গ্রুপ, যারা বিশ্বের দুর্গম ও সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে কর্মরত সাংবাদিকদের বিনা মূল্যে সুরক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তাদের প্রশিক্ষণগুলোর প্রথম দুদিন কোনো সংকট মোকাবিলায় সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর চার দিন থাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ। তাদের কর্মকাণ্ডগুলোতে সুযোগ পান অভিজ্ঞ, কর্মরত, ফ্রিল্যান্স ও আঞ্চলিক সাংবাদিকেরা। এটি প্রশিক্ষণগুলো আয়োজন করা হয় বিভিন্ন জায়গায় এবং কারা আবেদন করছে, সেটি দেখেও নির্ধারিত হয়।